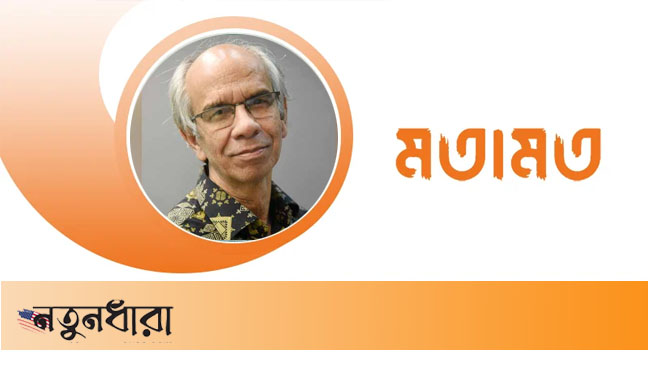
গোপালগঞ্জে যা ঘটেছে, তা শুধু দুঃখজনকই নয়—গভীর উদ্বেগের। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও যে ভবিষ্যতে আরও উত্তেজনা, এমনকি সহিংস সংঘর্ষের কারণ হতে পারে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে এমন এক সময় ঘটনাটি ঘটেছে, যখন জনগণের মাঝে একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠছে। এমন সহিংসতার পুনরাবৃত্তি হলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবে।
আরও একটা দিক উল্লেখযোগ্য। জুলাই শহীদদের স্মরণে যখন দেশজুড়ে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং ঠিক আবু সাঈদের মৃত্যুর দিনটিতেই, তখন এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যক্কারজনক ঘটনার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এটি এড়ানো যেত বলে আমি মনে করি।
গোপালগঞ্জের সহিংসতায় তিনটি পক্ষ জড়িত। প্রথমত, যারা এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে—জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তারা এক ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পদযাত্রা করে জেলায় জেলায় যাচ্ছিল। তাদের এই কর্মসূচি পূর্বঘোষিত, নিয়মতান্ত্রিক এবং আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হচ্ছিল।
আরেকটি পক্ষ এই সহিংসতার পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো গোপালগঞ্জের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশ—বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত। এদের মধ্যেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ, যাদের সেখানে সুসংগঠিত উপস্থিতি ও মাঠের শক্তি রয়েছে। তারা মুহূর্তের মধ্যে বড় জমায়েত করতে সক্ষম। অতীতে আমরা দেখেছি—এই ছাত্রসংগঠনটি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়েছে। পুলিশের সঙ্গেও তাদের এমন সংঘর্ষ ঘটেছে মাত্র কয়েক মাস আগে। এসব তথ্য প্রকাশ্য এবং প্রশাসনের কাছেও অজানা থাকার কোনো কারণ নেই।
এমন একটি পরিস্থিতিতে—যেখানে অস্থিরতা ও সংঘর্ষের ইতিহাস রয়েছে—সেখানে এনসিপির মতো একটি নতুন ও উদীয়মান রাজনৈতিক দলের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘাত দেখা দিতে পারে, সেটি অননুমেয় ছিল না। এই অনুমানকে উপেক্ষা করাই ছিল অবিমৃষ্যকারিতা।
তৃতীয় পক্ষ হলো সরকার—যার ওপর সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সব পক্ষের মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি জনজীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা। সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততা—এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে পক্ষগুলোর সংঘর্ষের চেয়ে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাও কম বিপজ্জনক নয়।
গোপালগঞ্জে আসার আগমুহূর্তে হঠাৎ করে তাদের কর্মসূচির নাম বদলে গিয়ে হয়ে গেল—‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’। কেন? মার্চ টু শব্দবন্ধটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই স্পর্শকাতর এবং প্রতীকী এক শব্দ। এর রেশ এখনো জেগে আছে ‘মার্চ টু ঢাকা’র মতো আন্দোলনের স্মৃতিতে, যা দেড় দশক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছে। সেক্ষেত্রে ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’—এটি কি নিছক পিরোজপুর থেকে গোপালগঞ্জের দিকে হেঁটে আসা? নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো বার্তা, ইঙ্গিত, এমনকি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল নিহিত?
এখন প্রশ্ন হলো—এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটাল কে? দায়টা মূলত কার? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই ঘটনাপ্রবাহে প্রাথমিক দায়ভার বহন করতে হবে এনসিপিকে। কারণ, তাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি যে একটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ—তা বোঝা যায়। তারা এক জেলার পর আরেক জেলায় পদযাত্রা করছে, এটা তারা আগেও করেছে। কিন্তু গোপালগঞ্জে আসার আগমুহূর্তে হঠাৎ করে তাদের কর্মসূচির নাম বদলে গিয়ে হয়ে গেল—‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’। কেন? মার্চ টু শব্দবন্ধটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই স্পর্শকাতর এবং প্রতীকী এক শব্দ। এর রেশ এখনো জেগে আছে ‘মার্চ টু ঢাকা’র মতো আন্দোলনের স্মৃতিতে, যা দেড় দশক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েছে। সেক্ষেত্রে ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’—এটি কি নিছক পিরোজপুর থেকে গোপালগঞ্জের দিকে হেঁটে আসা? নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো বার্তা, ইঙ্গিত, এমনকি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল নিহিত?
আমি মনে করি, এখানে ভাষার ব্যবহারে একটি প্রকাশ্য উসকানির চেষ্টা ছিল। এমন ভাষা এক ধরনের প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মতো, বিশেষ করে যখন গোপালগঞ্জকে ঘিরে আবেগ, ইতিহাস ও ক্ষমতার প্রতীক তৈরি করা আছে।
এনসিপি একটি নবীন দল। তাদের নেতৃত্বে তরুণরাই আছেন। এই অবস্থায় তাদের পক্ষ থেকে আরও দায়িত্বশীলতা আশা করা যেত। বিশেষ করে, যদি তারা স্পষ্ট করে বলত—‘আমরা জুলাই শহীদদের স্মরণ করছি, জুলাই আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের কাছে যাচ্ছি। গোপালগঞ্জবাসী, আমরা আপনাদের সঙ্গে সংলাপে আগ্রহী।’ তাহলে এক ধরনের সৌজন্যবোধ ও রাজনৈতিক শালীনতার প্রকাশ ঘটত।
কিন্তু তারা সেই পথ নেননি। বরং এমন ভঙ্গিতে তাদের অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালার মতো। আর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো—তাদের জানা ছিল, গোপালগঞ্জ একটি স্পর্শকাতর এলাকা, যেখানে উত্তেজনার ভিত্তি আগেই তৈরি হয়ে আছে। তবুও তারা এমন ভাষা ও কৌশল গ্রহণ করেছেন, যা সংঘাত সম্ভাবনাকে তীব্র করেছে।
গত কয়েক মাস ধরে আমরা লক্্যে করছি, জুলাই আন্দোলনের অনেক জোরালো সমর্থক, এমনকি কিছু প্রভাবশালী সংগঠক—বিশেষ করে যারা প্রবাসে অবস্থান করছেন এবং ইউটিউবার কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার পরিচয়ে পরিচিত—তারা ধারাবাহিকভাবে উত্তেজক ভাষায় কথা বলছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রভাব বাস্তব মঞ্চে—বিশেষ করে ঢাকায়—বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্ম দিচ্ছে।
এমনকি তাদের বক্তব্যে আমরা শুনেছি:
“৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি বা জাদুঘর ভেঙে ফেলতে পেরেছি, এবার আমরা তার মাজার ভাঙব”—এই ধরনের চূড়ান্ত উসকানিমূলক বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিষয়টি কোনোভাবেই অবহেলার নয়। যেখানে বঙ্গবন্ধুর কবর রয়েছে সেই গোপালগঞ্জ—তাকে ঘিরে যদি কেউ প্রতীকী বা প্রত্যক্ষ উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করে, সেটি সুশৃঙ্খল প্রতিবাদের অংশ নয়, বরং রাজনৈতিক উত্তেজনার বিস্ফোরক উপাদান।
এই প্রেক্ষাপটে, এনসিপি এবং সরকার—উভয়েরই সচেতন থাকা প্রয়োজন ছিল। গোপালগঞ্জ ঐতিহাসিকভাবে একটি স্পর্শকাতর স্থান। সেখানে রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজনের আগে একটি ন্যূনতম সাবধানতা ও কৌশলগত বোধ থাকা জরুরি ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের মাঝেই আমরা সেই সতর্কতা দেখতে পাইনি। বরং তারা যেন নিজেদের অবস্থানকে কেবল প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে।
এর বিপরীতে, আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের সব ধরনের কর্মকাণ্ড বর্তমানে নিষিদ্ধ, ছাত্রলীগও নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগের মাঠপর্যায়ের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবেই সক্রিয়। যদি তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া উসকানির পাল্টা দিতে গিয়ে গোপালগঞ্জের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—সরকার কি এই রকম একটা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকে অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছে?
সরকার আজ একটি বিবৃতি দিয়েছে—যেখানে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে, মতপ্রকাশের অধিকারে শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং যেসব সংগঠন নিষিদ্ধ, তারা যদি আইন ভঙ্গ করে তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বিবৃতি যদি ঘটনার আগেই আসত, তাহলে হয়তো পরিস্থিতির উত্তেজনা খানিকটা প্রশমিত হতো। প্রশাসনের দায়িত্ব শুধু ঘটনার পর বিবৃতি দেওয়া নয়, সম্ভাব্য সংকট প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি নেওয়াও।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো—এই গোপালগঞ্জকেন্দ্রিক ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনৈতিক উত্তেজনার যে বাতাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বইছে, তা শুধু এই একটি কর্মসূচি ঘিরেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো না কোনো মহল হয়তো এই উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কিংবা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করার চক্রান্তমূলক অভিলাষ লালন করছে।
এই কারণেই প্রত্যেক পক্ষ—সরকার, বিরোধী দল, নতুন রাজনৈতিক শক্তি, এমনকি সাধারণ নাগরিক—সবার সতর্ক, সংযত ও দূরদর্শী আচরণ এখন সময়ের দাবি।
আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু জনগণের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, গোপালগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এক ধরনের পরিকল্পিত উসকানি বা চক্রান্তের ফল, যার উদ্দেশ্য হতে পারে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা কিংবা পিছিয়ে দেওয়ার মতো একটি অস্থির পরিবেশ তৈরি করা—তাহলে তাদের এই সন্দেহকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা যাবে না। বিশ্বাসের এই ঘাটতি কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তির ওপর আস্থাহীনতারই প্রতিফলন।
তাই বারবার বলছি—যদি সরকার ও এনসিপি আগেভাগেই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করত, সংলাপের চেষ্টা করত কিংবা স্থানীয় প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে প্রস্তুত রাখত, তাহলে এমন একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব ছিল। এই সহিংসতায় চারজন নিহত হয়েছেন—এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এমন অনর্থক প্রাণহানি প্রতিহত করা যেত, যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দায়িত্ববোধ আগে থেকে দেখা যেত।
এই ঘটনার মধ্যেই আরও একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে—গোপালগঞ্জের এই সংঘর্ষের পর আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে কীভাবে পুনরায় মঞ্চে ফিরতে চায়? বিগত এক বছরে আমরা দেখেছি, দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় নেতা পলাতক, এবং সবাই জানে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লিতে আশ্রিত। দেশে অবস্থান করছেন মূলত মাঠপর্যায়ের কর্মী ও সমর্থকরা।
কিন্তু প্রশ্ন হলো—গত এক বছরে আওয়ামী লীগের এই মাঠপর্যায়ের তৎপরতা নেতৃত্ব থেকে কী ধরনের দিকনির্দেশনা পেয়েছে? কিংবা তারা আদৌ কোনো সুসংগঠিত রূপে রাজনীতিতে ফিরে আসবে কি না, সেই দিশা দলটি দেখাতে পেরেছে কি? গোপালগঞ্জের ঘটনা সেই প্রশ্নকে আরও জটিল ও জরুরি করে তুলেছে।
এনসিপি যেমন এখন পরীক্ষার মুখোমুখি, ঠিক তেমনই আওয়ামী লীগের সামনে এখন প্রশ্ন—তারা কি সংঘাতের মাধ্যমে না কি রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ফিরে পাওয়ার পথ খুঁজবে? এই উত্তরের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নির্ভর করতে পারে।
এটা বলতেই হবে—আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশের মানুষ নানা ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি এবং নির্বাচনের প্রতি অবিচারের শিকার হয়েছে। এই কারণেই মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ গড়ে উঠেছিল। সেই ক্ষোভই এক বছর আগে বহিঃপ্রকাশ পেয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন ঘটিয়েছে।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সময়ের এই রাজনৈতিক ব্যর্থতার দায় আওয়ামী লীগ কতটা স্বীকার করেছে? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকৃত আত্মবিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়নি। তারা জনসাধারণের কাছে এসে বলেনি, ‘আমরা ভুল করেছি, আমরা শুদ্ধ হই, আমরা নতুনভাবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে চাই।’ বরং তারা দাবি করছে, ‘আমরা ফিরে আসব, আর কেউ রক্ষা পাবে না, কেউ পালাতে পারবে না’। এমন শাসক-ভঙ্গি ও হুমকিমূলক বক্তব্য দেশের রাজনীতিতে অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। গোপালগঞ্জের মতো সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির পেছনে এরও অবদান অস্বীকার করা যায় না।
তাই প্রথমেই আওয়ামী লীগের উচিত তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভুলগুলো গভীরভাবে মূল্যায়ন করা, কেন তারা জনগণের রোষের মুখে পতিত হলো তা বিশ্লেষণ করা। কোনো ধরনের আত্মসমালোচনা ও অনুশোচনা ছাড়া পুনরায় রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসা সম্ভব নয়।
আরো গুরুত্বপূর্ণ, তাদের রাজনৈতিক কৌশল ও নেতৃত্বের পুনর্গঠন। বর্তমান অবস্থায় দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব পলাতক রয়েছেন, আর তরুণ কর্মী-সমর্থকরা মাঠে অবস্থান করছে। কিন্তু তাদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা বা তাদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলা মোটেও কাম্য নয়। নেতারা যদি সত্যিই দেশের রাজনীতি নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চান, তবে অবশ্যই দায়িত্বশীল ও মানবিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।
এখন প্রশ্ন হলো—গোপালগঞ্জের এই ঘটনা পরে আরও বড় ধরনের সংঘাত ও উত্তেজনার দিকে যাবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে বিভিন্ন পক্ষের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর।
ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, দেশের অনেক জায়গায়, ‘উত্তেজিত জনতা’ কিংবা ‘মবের ছদ্মবেশে’ কিছু রাজনৈতিক মহল—যারা মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতার জন্য কাজ করে—তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন, ব্যক্তির অধিকার হরণ এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মতো কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। অথচ সরকারের দৃষ্টি ও প্রতিক্রিয়া ছিল যথেষ্ট উদাসীন ও অপ্রতুল।
সরকার যদি এই ধরনের ঘটনা দমন করতে না পারে বা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, আবার কখনো কখনো সরকারি হস্তক্ষেপ এমনভাবে হয় যে, তা বিশৃঙ্খলা ও মব সন্ত্রাসকে আরও জোরালো করে, তাহলে এই ধরনের অবস্থা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
সুতরাং, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল হবে কিনা—তা পুরোপুরি নির্ভর করবে সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতার ওপর।
সূত্র: বিডি নিউজ