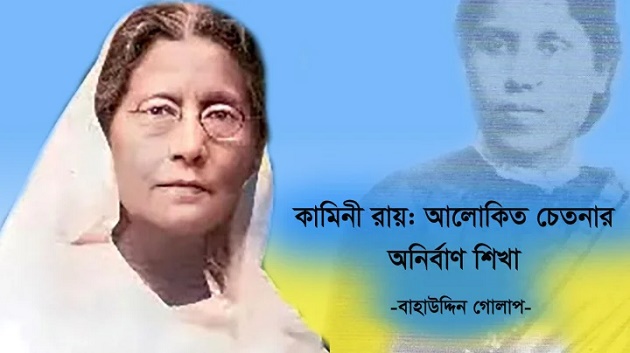
বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে যে কয়েকজন মহীয়সী ব্যক্তিত্ব সমাজের গতিহীন নদীতে নতুন স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন, কামিনী রায় তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। অন্ধকার থেকে আলোর, নিষেধ থেকে মুক্তির এবং নীরবতা থেকে সৃষ্টির যে মহাযাত্রা—তিনি ছিলেন তার এক অকুতোভয় পথিকৃৎ।
১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন বাকেরগঞ্জ অর্থাৎ বর্তমান ঝালকাঠি জেলার বাসণ্ডা গ্রামের এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা পরিবারে তার জন্ম হয়। পিতা চন্দ্রকুমার রায় ও মাতা অমৃতা রায়—উভয়েই ছিলেন তাদের সময়ের প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী, যাঁরা কন্যার শিক্ষা ও মানসিক বিকাশে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও সাহিত্য এক গভীর রূপান্তরের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ—এই সবকটি প্রগতিশীল ধারা মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল এক জটিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আবহ। আর এই পরিবর্তনেরই এক জীবন্ত ও সক্রিয় প্রকাশ ছিলেন কামিনী রায়। তার জন্ম হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে, যখন বাংলার নবজাগরণ পূর্ণ যৌবনে উপনীত, কিন্তু নারীমুক্তির প্রশ্নটি তখনও প্রান্তিক অবস্থানেই রয়ে গিয়েছিল।
কামিনী রায় কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে প্রথম বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন, যা তাঁকে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম নারী স্নাতকদের মধ্যে একজন করে তোলে। এর মাধ্যমে তিনি যে কেবল এক শিক্ষাগত মাইলফলক স্থাপন করেছিলেন তাই নয়, বরং প্রমাণ করেছিলেন নারীশিক্ষার অফুরান সম্ভাবনা। পরবর্তীতে তিনি সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন—যা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ সেই সময়ের জন্য। এই শিক্ষাজীবন তাঁকে শিখিয়েছিল যে, জ্ঞানার্জন কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয় বরং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।
সমকালীন সাহিত্য পরিমণ্ডলে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তার 'কপালকুণ্ডলা' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে নারীচরিত্র সৃষ্টি করছেন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই কামিনী রায়ের কাব্যচর্চা শুরু হয়। কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য ছিল তার নিজস্বতায়—তিনি লিখেছেন নারীর নিজস্ব ভাষায়, নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। বঙ্কিমের নারীরা যখন পুরুষের কল্পনার প্রতিমা, কামিনী রায়ের নারীরা তখন বাস্তবের জীবন্ত মানুষ—স্বপ্ন দেখা, সংগ্রামী, জিজ্ঞাসু। এই দার্শনিক পার্থক্য বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেছিল। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, যেখানে নারীমনের গভীরতম অনুভূতিগুলি প্রথমবারের মতো সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছিল। এই গ্রন্থেরই 'নারী' শীর্ষক কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন:
"নারী, তোরে আর অবহেলা নয়,
তোরে দিয়েই জাগিবে নবপ্রভাত"
এটি কেবল একটি কবিতার পঙ্ক্তি নয়, এটি ছিল এক দার্শনিক ইশতেহার, যেখানে নারীর মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নতুন সমাজের বীজ। এই কাব্যের নামটিই যেন হয়ে উঠেছিল তার সাহিত্যিক জীবনের দর্শনবাণী—আলো ও ছায়ার অনিবার্য সহাবস্থান, জ্ঞান ও অজ্ঞতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।
১৮৯৪ সালে কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কামিনী রায়। সংসার, সন্তান ও গৃহস্থালির নানা দায়িত্বের মধ্যেও তিনি নিরলসভাবে চালিয়ে গিয়েছেন সাহিত্যচর্চা। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নির্জনা'। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' লিখছেন। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের নারীরা প্রেম ও আত্মদানের প্রতীক, আর কামিনী রায়ের নারীরা আত্মসন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। এই গ্রন্থের 'অন্তরে' শীর্ষক কবিতায় তিনি আরও অন্তর্মুখী হয়ে আত্মানুসন্ধানের পথে যাত্রা করেছিলেন:
"চেয়ে দেখি অন্তরে, কত অন্ধকার!
তবু তারই মাঝে লুকানো আলোকের ঝরনা"
এই পঙ্ক্তিগুলির মধ্য দিয়ে তিনি মানবমনের জটিলতা ও সম্ভাবনাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে অন্ধকার আর আলোর দ্বন্দ্ব একটি গভীর আধ্যাত্মিক বোধের জন্ম দেয়—আত্মজয়ের মাধ্যমেই বাহ্যিক বাধা জয় করা সম্ভব। এই দার্শনিক উপলব্ধি বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল।
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' লিখছেন, নজরুলের আবির্ভাব হয়নি তখনও, আর প্রেমচন্দ হিন্দি সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করছেন। এই প্রেক্ষাপটে কামিনী রায়ের 'পরার্থে' কাব্য বাংলা সাহিত্যে এক নতুন নৈতিক চেতনার জন্ম দেয়:
"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"
এই বাণী কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, সামাজিক চিন্তাধারায় এক মৌলিক সংযোজন। এটি উপনিষদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা। এই দার্শনিক চেতনা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সামূহিকতার মধ্যে এক সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করে।
কামিনী রায়ের সাহিত্যকীর্তি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের কবিতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তার শিশুসাহিত্য রচনা বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'গুঞ্জন' শিশুকিশোরদের জন্য রচিত তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যেখানে তিনি শিশুমনের সরলতা ও কৌতূহলকে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও 'শিশুদের বুদ্ধিদীপক গল্প' এবং 'বালকবালিকাদের গল্প' শিশুদের জন্য তার রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য রচনায় তার বিশেষত্ব ছিল যে তিনি শিশুদের জন্য লিখলেও তার রচনায় দার্শনিক গভীরতা ও নৈতিক বোধের অভাব ছিল না। তিনি শুধু শিশুদের মনের তৃপ্তির জন্য নয়, বরং চরিত্র গঠন ও নৈতিক বিকাশের জন্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন।
তার গদ্যসাহিত্যেও সমাজচেতনা ও নারীবাদী দর্শনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। 'বালিকা শিক্ষা' প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তা তৎকালীন সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। তার 'নারীজাতির অধিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,
"শিক্ষাই নারীর মুক্তির একমাত্র পথ"
এটি এমন একটি চিন্তা যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী ছিল। এই গদ্যরচনাগুলি তার কবিতারই সম্প্রসারণ, যেখানে তিনি নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনচেতার দর্শনকে আরও সুসংহত রূপে উপস্থাপন করেছেন।
১৯২০-এর দশক বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সময়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, আর কলকাতায় নারী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এই সময়ে কামিনী রায়ের 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা পায়:
"সদা ভয়, সদা লাজ, সংশয় সম্ভ্রম করে,
এই তো জীবন বিসর্জন"
এই শব্দগুলিতে যে সামাজিক সমালোচনা, তা নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু ভিন্নতর। নজরুল বিদ্রোহ করছেন বাহ্যিকভাবে, আর কামিনী রায় বিদ্রোহ করছেন আভ্যন্তরীণভাবে। এটি ছিল এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যেখানে তিনি সমাজের কৃত্রিমতা ও ব্যক্তির স্বাধীনচেতার দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছিলেন।
তার সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার এই সামাজিক আন্দোলনগুলি তার সাহিত্যকর্মকে একটি বাস্তব ভিত্তি প্রদান করেছিল। তিনি বাংলার নারী আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেন এবং নারী শিক্ষা ও নারী অধিকারের জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৯ সালে তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে তার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি দেন। ১৯৩০ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন—এই পদে অধিষ্ঠিত প্রথম নারী হিসেবে। তার রচনাসমগ্রে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্য—সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ। তার 'দীপ ও ধূপ' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে জীবনসায়াহ্নের পরিপক্ব দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ পেয়েছে। তার 'আলোক' কাব্যের 'চিরদীপ' কবিতার বাণী বাংলার নারীসমাজের জন্য এক নতুন মন্ত্র হয়ে উঠে:
"চল, তোর পথে আলো জ্বালো,
তুই নিজেই হও চিরদীপ"
এই সময়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও নারীশিক্ষার জন্য কাজ করছেন, কিন্তু কামিনী রায়ের বিশেষত্ব ছিল তার দার্শনিক গভীরতায়। তিনি শুধু সমাজসেবী নন, তিনি প্রথম নারী যিনি সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর আত্মিক মুক্তির দর্শন রচনা করেছেন। এই চিরদীপ হওয়ার আহ্বান কোনো রূপক বাক্য নয়; এটি এক নৈতিক ও দার্শনিক আদেশ—যে আলো ব্যক্তির অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে সমগ্র সমাজকে আলোকিত করে। সমসাময়িক অন্যান্য নারী সাহিত্যিকদের তুলনায় কামিনী রায়ের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন তার আগের প্রজন্মের, কিন্তু তিনি মূলত উপন্যাস ও গান রচনা করেছেন। কামিনী রায় প্রথম নারী যিনি সুনির্দিষ্টভাবে কাব্যচর্চা করেছেন এবং নারীবাদী দর্শন বিকাশ করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের মহাশ্বেতা দেবী বা আশাপূর্ণা দেবীর তুলনায়ও কামিনী রায়ের ভূমিকা ভিন্ন—তিনি পথিকৃৎ, যিনি প্রথমবারের মতো নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্য রচনার সাহস দেখিয়েছেন।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ঝালকাঠির বাসণ্ডা গ্রামের তার পৈতৃক ভিটে দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে আজ কোনও স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এককালের একতলা বাড়ি, পুত্র অশোকের সমাধি, স্নানঘাটলা এবং অন্যান্য পুরনো স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০০৮ সালে বাড়িটি ভেঙে ফেলার সময়ে সংস্কৃতি কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছিলো। এরপরেও বিভিন্ন সময়ে কবির বসতভিটা দখলমুক্ত করে সেখানে স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক স্থানটি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ কখনোই গৃহীত হয়নি। এই ধ্বংসের ফলে হারিয়ে গিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা কামিনী রায়ের জন্ম ও শৈশবের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতিহীনতারই পরিচয় বহন করে। এখনই সময় এসেছে জাগরণের। কামিনী রায়ের বসতভিটা উদ্ধার এবং স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ নাগরিকদের একত্রিত হয়ে এই ঐতিহাসিক স্থানটি পুনরুদ্ধার করতে হবে। এখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে 'কামিনী রায় স্মৃতি সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র', যেখানে নতুন প্রজন্ম তার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবে, গবেষণা করতে পারবে।
কামিনী রায়ের জীবন ও সাহিত্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছে যে, মুক্তি অর্জন করতে হয় জ্ঞানে, পরিশ্রমে, নৈতিকতায় এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, নারী শুধু গৃহের আলোক নয়, সমাজের মশালবাহকও বটে। তার সৃষ্টিকর্ম ও চিন্তাধারা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিরকাল বাঙালির চেতনায় জাগরুক থাকবে। তার সৃষ্টিকর্ম আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আলো ও ছায়ার এই দ্বন্দ্বময় জীবনপথে, স্মৃতির ছায়াকে ডিঙিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আলোর দিকে। কারণ, সত্য, ন্যায় এবং মানবিকতা চিরন্তন। এরা নতুন প্রজন্মের অন্তরে জেগে উঠে, কামিনী রায়ের মতোই আলো ছড়ায়—প্রজ্জ্বলিত, অম্লান চিরদীপ হয়ে। তার এই আলোকযাত্রা বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
লেখক: ডেপুটি রেজিস্টার/ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়/[email protected]